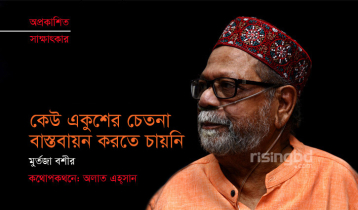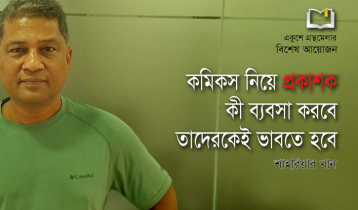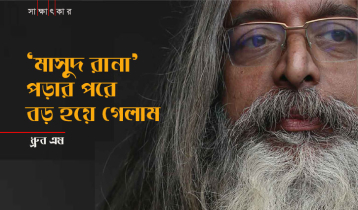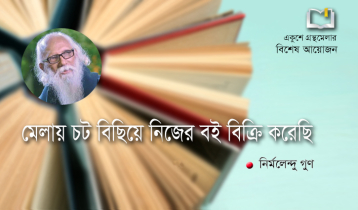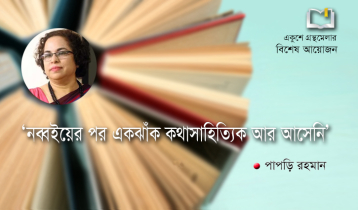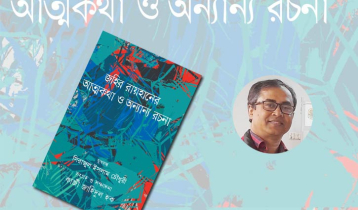রিজিয়া রহমানের ‘অগ্নিস্বাক্ষরা’ : কথাশিল্পীর শুভযাত্রা
কুমার দীপ || রাইজিংবিডি.কম

কুমার দীপ: আগস্টের কপালে আরেকটি মৃত্যুতিলক যুক্ত হলো। কথাসাহিত্যিক রিজিয়া রহমান (১৯৩৯-২০১৯) মারা গেলেন ১৭ আগস্ট। বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে নিহত হওয়ার কারণে এটা যেমন শোকের মাস, তেমনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, ক্ষুদিরাম বসু, নেতাজি সুভাষ, শামসুর রাহমানসহ অনেক সর্বজন শ্রদ্ধেয় বাঙালিও লোকান্তরিত হয়েছেন এ-মাসে। ফলে এই মাসকে যদি বাঙালির ট্র্যাজিক মাস হিসেবে অভিহিত করা হয়, তাহলে বাড়িয়ে বলা হয় না।
যে সময়ে মেয়েরা; বিশেষত বাঙালি মুসলিম মেয়েরা সাধারণ শিক্ষার বিশেষ সুযোগ পেতো না, সেই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নেয়া এবং সাহিত্যের মতো একটি স্বাধীন ও উদারভাবনাপ্রসূত বিষয়ে লেখালেখি করা এবং তাতে সাফল্যলাভ করা গুটিকতক লেখিকার ভেতরে রিজিয়া রহমান অন্যতম। তিনি বাংলাদেশের অগ্রগণ্য নারী কথাসাহিত্যিকদের একজন।
রিজিয়া রহমানের জন্ম ১৯৩৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর কলকাতার ভবানীপুরে। দেশভাগের পরে পরিবারের সাথে চলে আসেন পূর্ব-পাকিস্তান। বাবার বদলির চাকরির সুবাদে ভারত ও বাংলাদেশের অনেক স্থান ঘুরে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন প্রথম বয়সে, ফলে লেখালিখিতে তা একটি মূল্যবান অভিজ্ঞতা হিসেবে কাজে দিয়েছে। ফরিদপুরে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করা রিজিয়ার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বাবার অকালমৃত্যুতে। পরে প্রাইভেটে মাধ্যমিক পাশ করে স্বামীর সঙ্গে পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে উচ্চমাধ্যমিকের পড়ালেখা করেন। অবশ্য মাইগ্রেশন সম্পর্কিত জটিলতার কারণে ঢাকার ইডেন মহিলা কলেজ থেকেই উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করতে হয় তাঁকে। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন অর্থনীতি বিষয়ে।
‘ত্রিভূজ’ নামে একটি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন রিজিয়া রহমান। পরবর্তী কালে জাতীয় জাদুঘরের পরিচালনা বোর্ডের ট্রাস্টি এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কার্য-পরিচালকের পদে চাকরি করেন। বাংলা একাডেমির কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন তিন বছর।
আরও অনেক সাহিত্যিকের মতো শৈশবে কবিতা দিয়েই লেখালিখির হাতেখড়ি হয়েছিল রিজিয়া রহমানের। তবে ঔপন্যাসিক হিসেবেই তিনি সমধিক স্বীকৃত। ২৫টির অধিক উপন্যাস রচনা করেছেন রিজিয়া, তন্মধ্যে ‘উত্তর পুরুষ’(১৯৭৭), ‘বং থেকে বাংলা’(১৯৭৮), ‘রক্তের অক্ষর’(১৯৭৮), ‘অলিখিত উপাখ্যান’(১৯৮০), ‘ধবল জ্যোৎস্না’(১৯৮১), ‘একাল চিরকাল’(১৯৮৪) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অবশ্য রিজিয়া রহমান তাঁর সাহিত্যিক আবির্ভাব জানান দিয়েছিলেন ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে, ক্লাস ফাইভের ছাত্রী থাকা অবস্থায় কলকাতার ‘সত্যযুগ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ‘টারজান’ নামে একটি ছোটদের গল্প।
ত্রিকালদর্শী (ব্রিটিশ-পাকিস্তান-বাংলাদেশ) এই লেখিকার প্রথম গ্রন্থ ‘অগ্নিস্বাক্ষরা’ প্রকাশিত হয়েছিল আশ্বিন ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে (১৯৬৭ খ্রি.)। গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রে বলা হয়েছে: ‘আমার সত্যাশ্রয়ী আব্বার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে; আর পৃথিবীর দুঃখের ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে স্নেহের ডানার আড়াল করে আমাদেরকে বড় করেছেন যিনি, আমার সেই আম্মাকে।’ অধিকাংশ বাঙালি সন্তানই তার প্রথম প্রিয় কাজটি বাবা-মাকেই নিবেদন করতে চান। সেটাই স্বাভাবিক; যেহেতু তাদের নিকটেই সন্তানের সর্বোচ্চ ঋণ। গ্রন্থমধ্যেও ঋণ স্বীকারের স্বাক্ষর রয়েছে একাধিক গল্পে। এই ঋণ কোনো ব্যক্তিঋণ নয়, ইতিহাসের ঋণ; নৃতাত্ত্বিক পৃথিবীর ঋণ। ‘অগ্নি-স্বাক্ষরা’, ‘সিন্ধু-পতন’, ‘প্রেম একটি নদী’, ‘অনন্যা পৃথিবী’, ‘সমুদ্র-প্রিয়া’, ‘নির্জন প্রহর’, ‘কার্পেট’, ‘মৌন আকাশ’, ‘এক কান্নার স্বাদ’, ও ‘লাল টিলার আকাশ’ শিরোনামের ১০টি বিবিধ স্বাদ ও প্রকৃতির গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে এই সংকলন। গল্পপ্রিয় পাঠকের জন্যে তো বটেই, ইতিহাস-ঐতিহ্য-নৃতত্ত্ব সচেতন মননের জন্যেও অনিন্দ্য আয়োজন এটি।
প্রসঙ্গত, গল্পগুলো ধরে ধরে ঈষৎ আলোকপাতের চেষ্টা করি।
অগ্নিস্বাক্ষরা: ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তৈরি গল্প। পলাশীযুদ্ধের পর বাংলার মুসলমানদের যে দুরবস্থা হয়েছিলো, তারও কিছুটা নমুনা আছে। ইংরেজদের সহযোগী হিসেবে এদেশের জমিদাররা, বিশেষত হিন্দু জমিদারদের অনেকেই প্রচণ্ড অত্যাচারী হয়ে উঠেছিলেন- তার ছবিও এগল্পে আছে। কিন্তু যে বিষয়টি সবচাইতে গুরুত্ব নিয়ে আছে তা হলো একটি সাধারণ মুসলিম রমণীর ঘরে-বাইরে বিদ্রোহী হয়ে ওঠা, বিদ্রোহী হয়ে অত্যাচারী জমিদার ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করে; সংগ্রাম করতে করতেই আত্মাহুতি দেওয়া। কিন্তু গল্প পড়তে পড়তে, এর বিস্তৃত পরিসর, মূল গল্পের সাথে শিথিল সম্পর্কযুক্ত বিবিধ ও বিচিত্র ঘটনার উপস্থাপন আর বয়ানরীতি দেখে ‘অগ্নিস্বাক্ষরা’ গল্পটি কি ছোটগল্পের শৈল্পিক পরিমিতিবোধকে ঠিকমতো ধারণ করতে পেরেছে কি না এমন প্রশ্নও উঠতে পারে।
গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র গুলনাহার। জমিদার কৃষ্ণকান্তের নায়েব মেশের আলীর স্ত্রী। পিতার গুরুতর অসুস্থতার খবরে মেহেরপুর থেকে বাঁশবাড়িতে যাওয়ার পথে বিশ্বস্ত গাড়োয়ান রাজীব লোচনের আন্তরিকতায় নীলকুঠির সাহেবের লোকজনদের লাঞ্ছনার হাত থেকে রেহাই পেলেও বাড়ি পৌঁছে পিতাকে সে আর জীবিত পায় না। ইংরেজ সাহেবের হুকুম মতো নীলচাষে রাজি না হওয়ায় কুঠির লাঠিয়ালরা গুলনাহারের পিতা সৈয়দ আক্কাসকে এমনই প্রহার করে যে, কয়েকদিনের ভেতরে তার মৃত্যু হয়। পিতার এই করুণ মৃত্যুই গুলনাহারকে আমুল পাল্টে দেয়। সে কেবল ইংরেজদের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহী হয় না, এই পাশবিকতার প্রতিশোধ না নিয়ে স্বামীর বাড়িতে না ফেরার মতো ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করে বসে। প্রতিশোধ পরিকল্পনায় সঙ্গে পায় বাল্যবন্ধু হায়দারকে। হায়দারের ওস্তাদ বিখ্যাত সংগ্রামী তিতুমীরেরও পরোক্ষ পরামর্শ আসে তার কাছে। সঙ্গে নিতে সমর্থ হয় গ্রামের সাধারণ নারী-পুরুষকেও। এদিকে মেশের আলীর অর্থ ও ক্ষমতার লোভের সুযোগ নিয়ে জমিদার কৃষ্ণকান্তও গুলনাহারকে নিয়ে ফুর্তি করবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। তারা দুজনেই গুলনাহারকে সাহায্য করবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাতের অন্ধকারে নিরীহ জনতার উপরে লেলিয়ে দেয় সশস্ত্র ইংরেজ বাহিনীকে। অসংখ্য গ্রাম্য জনতার সাথে গুলনাহারের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু, যাকে সে একসময় ভালোবাসতো, সেই হায়দার নিহত হয়। ধৃত গুলনাহারকে কৃষ্ণকান্তের বাগানবাড়িতে এনে রাখা হয় বিরংসা চরিতার্থ করবার জন্যে। ছদ্মবেশী রাজীব এসে তিতুমীরের আগমনবার্তা দিয়ে যায় গুলনাহারকে। কিন্তু তার আগেই এক রাতে কৃষ্ণকান্তের লোলুপ আক্রমণের স্বীকার হওয়া গুলনাহার নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে সেই আগুনেই পুড়িয়ে মারে কৃষ্ণকান্তকে। বাংলার কৃষকবিদ্রোহের এক অগ্নিস্বাক্ষর বহন করে বলেই গুলনাহারের এই আগুনঝরা সংগ্রামকে ‘অগ্নিস্বাক্ষরা’ হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন গল্পকার।
এমন একটা প্রতিশোধের আগুনে শেষ হওয়ায় কিছুটা স্বস্তি হয়তো লাগে, কিন্তু ছোটগল্প না কি কোনো ক্ষুদ্র উপন্যাস পড়েছি, এমন অস্বস্তিও সুপ্ত থাকে না। পরিধি দীর্ঘ; এটা মেনে নিলেও ঘটনা-অনুঘটনার বৈচিত্র্য, অল্পপ্রাসঙ্গিক বা অনিবার্য নয় এমন ঘটনার বর্ণনা, এবং বর্ণনারীতির পরিমিতিবোধের অভাব কিছুটা পীড়িত করে বৈকি। তবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনায় রিজিয়া রহমানের কুশলতার পরিচয়ও পাঠকের নজর কাড়ে। যেমন : ‘গ্রাম ছাড়িয়ে ক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে জমিদারের পাল্কী চলেছে। পাল্কীর খোলা দরজা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি মেলে রেখেছেন কৃষ্ণকান্ত রায়। হলুদ বৃন্ত চৈতী শস্যের প্রান্তরে রৌদ্রোজ্জ্বল অপরাহ্ণ সুরাপাত্রের মত গাঢ় নেশার রঙ ছড়িয়েছে।’
গল্পের আরও একাধিক স্থানে লেখকের ভাষায় বাংলার প্রকৃতি শব্দমূর্তি লাভ করেছে। তবু এই গল্পের ইতিহাস সচেতনতাই পাঠককে হয়তো অধিক আকৃষ্ট করে। ব্রিটিশ বাংলায় কৃষিজীবী মানুষেরা পরাধীনতার নাগপাশে কীভাবে পর্যুদস্ত হতো, তাদের জীবনে কীভাবে নেমে আসতো নীলকর সাহেবদের অত্যাচার; তার গল্পায়ন করতে গিয়ে নর-নারীর প্রেম, সংসার প্রভৃতি বাঙালি মুসলমানের সেসময়কার সাধারণ যাপিত জীবনও তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন রিজিয়া রহমান। এবং একজন নবীন গল্পকার হিসেবে এজায়গাটিতে তাঁর কৃতিত্ব প্রশংসার দাবি রাখে।
সিন্ধু-পতন: সিন্ধু সভ্যতা শুধু ভারতবর্ষেরই নয়, পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস ও সভ্যতার এক অসামান্য নিদর্শন। নাম দেখে সিন্ধু সভ্যতার অন্তিম মুহূর্তের দৃশ্যধৃত কাহিনির কথা মনে হলেও এটি যতটা সিন্ধু সভ্যতার পতনের কাহিনি, তার চাইতে ঢের বেশি প্রেমের। সিন্ধু সভ্যতার পতনমুহূর্তের কিছুটা কল্পিত বিবরণ থাকলেও গুরুত্ব পেয়েছে নর-নারীর প্রেম; শরীরী মোহ। সিন্ধু নগরীর প্রখ্যাত নর্তকী ইনলার সঙ্গে দূরের ওকরি গ্রামের কুমোরপুত্র শিবার্ক-এর প্রেম নিছকই দুর্ঘটনাজনিত। জলসার আসর শেষে গভীর রাতে ফেরার পথে নিজের রথের নিচে চাপা পড়ে আহত হওয়া শিবার্ককে গৃহে এনে সেবা-শুশ্রুষা করবার এক পর্যায়ে একে অপরের প্রেমে পড়ে যায়। চাইলেও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিলীন ওকরি গ্রামে পুনরায় বসতি স্থাপন করতে না পারা শিবার্ক ইনলার বদৌলতেই নগরীর বাঁধ রক্ষকের চাকরি পায়। দুজনের ভেতরেই ঘর বাঁধার স্বপ্ন জাগে। কিন্তু দুজনের মনেই তৈরি হয় প্রতিবন্ধকতা শিবার্ক চায় ইনলা একমাত্র তার হোক, নর্তকীর পেশাটা ছেড়ে দিক। কিন্তু যে জিনিসের জন্যে এমন খ্যাতি-পরিচিতি; উচ্চসমাজে মূল্য; সেই নর্তকীরূপকে ত্যাগ করা ইনলার পক্ষে সম্ভব হয় না। বহু প্রতীক্ষিত যে পূর্ণিমা রাতে ইনলা-শিবার্কের দাম্পত্য জীবনের শুরু হওয়ার কথা ছিলো, সেই রাতে আগত বিদেশি অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্যে তাদের বাণিজ্যজাহাজে যায় ইনলা। সিন্ধুরাজার আদেশে, দেশের মঙ্গলের জন্যই তাকে এটা করতে হয়। কিন্তু শিবার্ক-এর প্রেমিক মন প্রচণ্ড অভিমানী হয়ে বিধ্বংসী রূপ নেয়। ক্ষুব্ধ শিবার্ক মুহূর্তেই আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যে জলোচ্ছ্বাস থেকে নগরীকে বাঁচানোর দায়িত্ব ছিলো তার, সেই জলোচ্ছ্বাসের মুখেই বাঁধের ইট খুলে দিয়ে নগরীকে সিন্ধুর জলে ভাসিয়ে দিলো সে।
এভাবে সিন্ধু নগরীর ধ্বংসের যে চিত্র গল্পকার তৈরি করেছেন তার ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে সংশয় আছে। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে শুরু হওয়া এবং প্রায় চার হাজার বছর আগে ধ্বংসপ্রাপ্ত সিন্ধুসভ্যতার সন্ধানসূত্র উনিশশতকের হলেও এর আবিষ্কার ও খননকার্য বিশশতকের দ্বিতীয় দশকে শুরু হয়। শিক্ষিত সাধারণ মানুষের কাছেও এর ইতিহাস বেশ পরের এবং অস্পষ্ট একটি বিষয় হয়েই ছিলো। ১৯২০ সালের দিকে শুরু হওয়া খননকাজ চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে মোটামুটি স্পষ্ট ধারণা দিলেও, এখনও এই সভ্যতা নিয়ে গবেষণা শেষ হয়নি। মাত্র কয়েকবছর আগে পাঁচবছরব্যাপী পরিচালিত এক জাপানি গবেষণাতে আজকের পৃথিবীর পার্সপোর্টের কার্য সম্পাদনের উপযোগী অভিজ্ঞান এর সন্ধান পাওয়া গেছে সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন বিশ্লেষণে। অভিভূত হওয়ার মতো আরো অনেক বিষয়াদি ছিলো সিন্ধু সভ্যতার প্রাণ।
সিন্ধু নগরী বন্যাকবলিত ছিলো, এটা ঠিক; কিন্তু সিন্ধুর পতনের জন্যে বন্যাই শুধু দায়ী কি না, এব্যাপারে গবেষকদের ভেতরে ভিন্নমত রয়েছে। দীর্ঘদিনের বিশৃঙ্খলা, নেতৃত্বের দুর্বলতা, প্রতিরক্ষার অপ্রতুলতা, কৃষির অপর্যাপ্ততা সিন্ধুসভ্যতাকে নাজুক করে ফেলেছিলো। এ অবস্থায় বিদেশি আর্যরা সহজেই সিন্ধুকে আক্রমণ ও সভ্যতাকে ধ্বংস করে তাদের আর্য-সভ্যতাকে দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। আধুনিক গবেষকদের অনেকেই এই মত সমর্থন করেন। কেউ কেউ মনে করেন ঘনো ঘনো বন্যা হওয়ার এক পর্যায়ে সিন্ধুবাসীরা বাড়ি-ঘর ভালোভাবে মেরামতের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এরপর আবার বৃষ্টি কমতে কমতে খরা শুরু হলে কৃষিনির্ভর এই সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু ধ্বংস যেভাবেই হোক, ‘সিন্ধুপতন’ ইতিহাস নয়, ইতিহাসাশ্রয়ী ছোটগল্প। ইতিহাসের সত্য অপেক্ষা লেখকের কল্পিত শিল্পসত্যই অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। আর যে সময়ে বসে তিনি লিখেছেন, সেসময়েও হয়তো এর থেকে বেশি জানবার মতো ছিলো না তাঁর পক্ষে। তাছাড়া আরেকটি বড়ো সত্য হলো, ‘সিন্ধুপতন’ আসলে প্রেমের গল্প; সিন্ধুর পতন অনেকটা উপলক্ষ্যমাত্র।
প্রেম একটি নদী: মানবসভ্যতার বিবর্তনধারাপ্রসূত কাহিনি এটি। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের বাংলাদেশের একটি মেয়ে রোখসানা তার দুই সহপাঠী-বন্ধু ইনাম ও জাফরের নিকট থেকে একই সময়ে প্রণয়ের আহ্বান পেয়ে কিছুটা দ্বিধান্বিত। নারী-পুরুষের আবহমান কালের আকাঙ্ক্ষার কথা ভাবতে গিয়ে সে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ফিরে গেছে মানবের প্রাচীন পৃথিবীতে।
আদিম অরণ্যদিনের সে পৃথিবীতে জাফর-ইনামদের জায়গা নিয়েছে ভলবা-ইরিচ নামের দুই প্রণয়াকাঙ্ক্ষী যুবাপুরুষ। রোখসানা ধরা দিয়েছে পুরুষদের প্রণয়লিপ্সার আধার রূপসী ইমা রূপে। প্রাচীন কালের সেই পুরুষদ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে ভিন্ন গোত্রের অধিকতর চতুর ও শক্তিশালী যুবক ইরিচ। প্রাচীন পৃথিবীর এই শরীরীমোহজাত দ্বন্দ্ব শেষ হওয়ার সাথে সাথে রোখসানার স্বপ্নও শেষ হয়েছে। তার মনে হয়েছে, ‘কল্পনার জগৎ থেকে এক টুকরো প্রেমের গানের সুর ভেসে এসেছিল। শাশ্বত চিরন্তন সেই নদী থেকে।’ অর্থাৎ নারী-পুরুষের প্রণয়ের বিষয়টি যে চিরকালীন; চিরন্তন নদীর মতোই যে তার ধারা আবহমান কাল ধরে বহমান; সেই কথাটাই বলতে চেয়েছেন কথাশিল্পী রিজিয়া রহমান। বলবার ভাষাটি সাধারণ এবং সুখপাঠ্য। সে সময়কার উপযোগী প্রকৃতি ও অন্যান্য অনুষঙ্গাদির বর্ণনায়ও লেখিকার কৃতিত্ব উল্লেখ করবার মতো।
অনন্যা পৃথিবী: পৃথিবী আর পৃথিবীর রমণীরূপের প্রতি আকর্ষণবোধ। রমণী শরীরের প্রতি প্রণয়াকাঙ্ক্ষা যে সাধারণ সংযমী পুরুষকেও যে কোনো সময় কাবু করে ফেলতে পারে, তার একটি উদাহরণ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র এরসাদ। এরসাদ জিওলজিস্ট। দুর্গম পাহাড়ে ভ্রমণ আর ফসিল কুড়োনোর নেশার সাথে রয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি মোহনীয় টান। অনন্য প্রকৃতির অসামান্য সৌন্দর্যশোভিত এক পূর্ণিমা রাতে আদিম উদ্দীপনায় মোহগ্রস্ত হয়ে যাযাবর কন্যা জালীনের ঠোঁটে বন্য চুম্বন এঁকে দেয় এরসাদ। হয়তো মেয়েটির ভেতরেও সে আহ্বান ছিলো। কিন্তু সেরাতেই স্ত্রী লতিফার আগমনের খবর পেয়ে এরসাদের মনে শুরু হয় দ্বিধা। যাযাবর মেয়েটি হয়তো ভাবেনি যে, তার শরীরে উষ্ণতা দেওয়া পুরুষটির স্ত্রী থাকতে পারে। তাই লতিফার আগমনে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। এরসাদের মনে সামান্য অনুশোচনা জন্মালেও খুব দ্রুতই তা শেষ হয়েছে স্ত্রী লতিফার বুকে স্বাভাবিক আশ্রয় গ্রহণের ভেতর দিয়ে। যেন কোথাও কিছুই হয়নি ! কারো মৃত্যুর জন্য তার কোনো দায় নেই ! লতিফার কাছে আগের সেই প্রিয় পতি সে !
একদিকে যেমন আনকোরা নর-নারীর শরীরী রোম্যান্স আছে অন্যদিকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-সভ্যতার স্বাভাবিক চিত্র উঠে এসেছে অবলীলায়। নামকরণের মাধ্যমে হয়তো লেখিকা বোঝাতে চেয়েছেন- ছোটো-খাটো এক-আধটি সমস্যার পরেও পৃথিবীটা সুন্দর।
সমুদ্র প্রিয়া: ষোড়শী তরুণী লিলির অস্বাভাবিক সমুদ্রপ্রেমের গল্প। যে বয়সে যুবাপুরুষের আগমনে মনের ভেতরে নবতরঙ্গের ঢেউ লাগার কথা, সেই বয়সে সমুদ্রের নীল জল আর তার ঢেউ লিলির হৃদয়কে অসম এক প্রণয়াবেগে মোহগ্রস্ত করেছে। সমুদ্রের নীল জলের প্রতি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ তাকে বিকারগ্রস্ত করেছে। চাকরিসূত্রে সমুদ্রতীরবর্তী একটি বাড়িতে ভাড়ায় থাকা বড়ো ভাইয়ের কাছে থেকে সাগরের নীল জলরাশি দেখতে দেখতে যে অসামান্য মুগ্ধতা তৈরি হয় লিলির, সেটা স্বাভাবিক; কিন্তু আস্তে আস্তে তা যখন বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছে যায়; টগবগে যুবক অপেক্ষা নিষ্প্রাণ জলরাশি তার ভালোবাসার কেন্দ্র হয়ে ওঠে; তখন অস্বাভাবিক বলেই সন্দেহ হয়। এবং এই সন্দেহকে সত্য প্রমাণিত করতেই যেন বড়ো ভাইয়ের পছন্দের ছেলেটি যথেষ্ট সুন্দর আর উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাকে বিবাহের পরিবর্তে সমুদ্রের বুকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জনের পথ বেছে নিয়েছে লিলি। অনাকাঙ্ক্ষিত ও অস্বাভাবিক প্রণয়স্পৃহার বলী লিলি সমুদ্রপ্রিয়া হওয়ার গল্প পাঠককে ব্যথিত করে বটে।
কোনো অস্বাভাবিকতাই শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত স্বাভাবিক পরিণতি বয়ে আনে না- একথাই হয়তো বলতে চেয়েছেন রিজিয়া।
নির্জন প্রহর: পুরনো প্রেমের স্মৃতি জাগানিয়া। স্বামীর সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে পরিচয় ! ঠিক পরচিয় নয়, পুনঃপরিচয়। রোম্যান্টিক কাহিনি বটে।
নীলি-হারুন দম্পতির পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়ার বিষয়টি স্বাভাবিক; কিন্তু বেড়াতে গিয়ে গাড়ি বিগড়ে যাওয়া এবং এরই প্রেক্ষাপটে নীলির পুরোনো প্রেমিক সাদিকের সাহায্য নিয়ে তারই বাসায় ওঠা; কিছুটা পরিকল্পিত বটে। তবে পরিকল্পিত দুর্ঘটনা শিল্প-সাহিত্যে-চলচ্চিত্রে স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। তাছাড়া নীলি তথা নীলার প্রেমাস্পদ; যার সাথে নীলির বিয়ের সমস্ত ব্যবস্থাই প্রায় চূড়ান্ত হয়ে ছিলো, সেই সাদিক বর্তমানে যেহেতু বনবিভাগে কর্মরত, সেহেতু পাহাড়ে বেড়াতে এলে তার সাথে যে কারোরই দেখা হয়ে যেতে পারে। দুজন পূর্ব-পরিচিত মানুষমাত্রই যেখানে অনেক দিন পরে সাক্ষাৎ পেলে একে অপরের অনুপুঙ্খ খবর নেওয়ার চেষ্টা করে, সেখানে দুজন প্রেমিক-প্রেমিকার দেখা হলে তো পুরোনো স্মৃতির জাগরণপূর্বক আবেগাপ্লুত হওয়ারই কথা। কিন্তু সেরকম কিছু হয়নি, বরং নীলি-সাদিক উভয়কেই অনেক সংযমী বলে মনে হয়েছে এ গল্পে। আগেই সন্দেহ করবার পরে সাদিকের বাসার নেমপ্লেটটা দেখে নীলি পাথরের মতো হয়েছে। সাদিক যখন নীলা বলে ডেকেছে তখন সে ডাক ‘বিষের পেয়ালার মত যন্ত্রণাময় বেদনানীল’ হয়ে ধরা দিয়েছে নীলির কাছে। সাদিক; যে এককালে কবিতা লিখতো বিলাসিতার মতো, সেই বিলাসের জন্যেই হয়তো একদিন যাকে সে হাত বাড়ালেই পেয়ে যেতো, সেই নীলাকে অবহেলা করেছিলো- এরকমই মনে হয় নীলির। অরণ্য প্রকৃতির মানবশূন্য নির্জনতায় সেই সাদিকের ভেতরেই জেগে উঠেছে নতুন প্রণয়স্পন্দন। সেই স্পন্দনের অনুরণন নীলা বা নীলির ভেতরেও যে জাগেনি, তা নয়; কিন্তু নীলি সেটার প্রকাশে সাবধানী। আর দশটা বাঙালি নারীর মতোই পুরোনো প্রেমিক অপেক্ষা স্বামী-সংসার তার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাই হারুণকে হরিণ শিকারে পাঠিয়ে দিয়ে সাদিক যখন কিছুটা সময় নীলার সঙ্গে কাটানোর জন্যে ফিরে এসেছে, তখন নীলা বলেছে, ‘জীবনটা নাটক নয় সাদিক। আর ভেব না আমিও জীবনকে তোমার মতো কবিতার বই মনে করি। ছিঃ তোমার লজ্জা হলো না। না হয় বিপদে পড়ে তোমার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি। তাই বলে তুমি আমার স্বামীকে শিকারের ছলে সরিয়ে দিয়ে আমার সঙ্গে প্রেমালাপের সুযোগ খুঁজছ...।’ অবশ্য এই সংযমের কৃত্রিম রেশও থেমে গেছে তার। সাদিকের একাকী জীবনের জন্যে সহানুভূতিও জেগেছে মনে। ভেবেছে, ‘আমি তো সবই পেলাম জীবনে। আর সাদিক? কি দিলাম ওকে! কি পেলও! এই নিঃসঙ্গ জগতে এক বুক বেদনা ছাড়া আর কি পেল ও!’ কেবল হাহাকারই নয়, ছল ছল চোখে বরং সে অভাবিতপূর্ব আবেগও ব্যক্ত করেছে। বলেছে, ‘আমি আর ফিরে যাবো না সাদিক। এই নিরালা পৃথিবীতে আমাকেও থাকতে দাও। কোনোদিন আর ফিরে যেতে বলো না।’ কিন্তু সাদিকও ক্ষুদ্রমতি নয়, আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করতে অপরের সংসারকে ভেঙে দেওয়া তার বিবেকজাত নয়। ঠোঁটের কোণে বিষণ্ন হাসি ফুটিয়ে নীলাকে বলেছে, ‘তোমার যে একটা সুখী বিবাহিত জীবন আছে- সেটা আমি জানি। ঘরে যাও নীলা।’ এখানে কেবল তাদের মুখের কথাই শেষ হয়নি, শেষ হয়েছে মূল গল্পটিও। পরের দিন সকালে স্বামীর সঙ্গে নীলির ফিরে যাওয়ার দৃশ্যটি শুধু সাধারণ পাঠকের দীর্ঘশ্বাস বাড়িয়েছে মাত্র।
কার্পেট: ‘কার্পেটের নিচে ধুলো বালি চাপা পড়ে। তাতে স্বাস্থ্যহানির কারণ ঘটে।’ গল্পের শেষদিকের এই বাক্য দুটি বলে দেয়, কার্পেটের সৌন্দর্য নয়, তার আড়ালে হারিয়ে যাওয়া সমাজের কোনো রুঢ় বাস্তবতার দিকেই ইঙ্গিত করতে সচেষ্ট হয়েছন গল্পকার। আহমেদ নামের এক তরুণ মাইন ইঞ্জিনিয়ারের আত্মকথনে সেই সময়ের এদেশীয় কয়লা খনির শ্রমিকদের মানবেতর জীবন ও ব্যক্তিস্বার্থনির্ভর আয়েশী জীবনের চালচিত্র তুলে ধরেছেন রিজিয়া রহমান। বিশ বছরের চাকরি জীবনে তরতর করে এগিয়ে যিনি ইস্টার্ন জয়েন্ট কোল কোম্পানির ম্যানেজার হয়েছেন, তিনি মনে করেন, ‘অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি- ওকথা মেনে চলে নেহাত গবেট হাবা যারা তারাই।’ ধূর্ততা ও শঠতাময় কর্মজীবন সততার তোয়াক্কা করে না। এবং তোয়াক্কা না করেই দিব্বি ভোগবিলাসী জীবনে মত্ত থাকতে পারে তারা। অন্যদিকে সমাজের যারা শ্রমজীবী মানুষ, কায়িক পরিশ্রমই যাদের প্রধান সম্বল, তারা দিনান্ত খেটেও পেটের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। কাজ করতে গিয়েই তারা কর্তাদের গাফিলাতি আর অব্যবস্থাপনার কবলে পড়ে অপঘাতে নিহত হয়, কিন্তু তার কোনো ক্ষতিপূরণ পায় না বিপর্যস্ত স্বজনেরা। প্রতিকার তো নয়ই, অন্য শ্রকিদের জন্যেও নেওয়া হয় না কোনো উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা। শ্রমিকেরাও জানে তাদের পরিণতি, কিন্তু কাজ ছেড়েও কোথাও যাওয়ার ক্ষমতাও থাকে না তাদের। বেশ দরদ দিয়েই লেখিকা তুলে ধরেছেন কয়লা শ্রমিকদের জীবনের অপ্রাপ্তি আর বেদনার গল্প। ছোটগল্প হিসেবে এর সমাপ্তিটা প্রশংসার দাবি রাখে।
মৌন আকাশধ: একটি অস্বচ্ছল ক্ষুদ্রচাকুরে পরিবারের মেয়ে হওয়ার মর্মপীড়া ও মর্মান্তিক পরিণতির কাহিনি। রেবা ও রেখা নামের দুই বোনের মধ্যে বড়ো বোন রেখার পড়ালেখা হয়নি বলে পরিবারে তার গুরুত্বও ছিলো অপেক্ষাকৃত কম। যে ছোট্ট একটি কক্ষের যে জানালা দিয়ে দু’বোন এক চিলতে আকাশ দেখবার সুযোগ পেতো, সেই জানালাই যেন তাদের জীবনের শত্রু হয়ে ওঠে। কোনো এক বখাটে ছেলের সাথে রেখার ভাব বিনিময় করবার অভিযোগে বাবার হাতে জানালাটা বন্ধ হয়ে গেলে রেবা খুব রেগে যায় আপুর উপরে। কিন্তু এরপর যখন অশিক্ষিত আইবুড়ো মেয়েকে এই সময়ে বিয়ে দেওয়ার প্রাণান্ত চেষ্টায় আকবর সাহেব পাত্রপক্ষের যৌতুকের দাবি মেটাতে শেষ সম্বল জমিটুকু বিক্রি করবার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলে ঘটে দুর্ঘটনা। বাবা-মাকে দুশ্চিন্তামুক্ত করতে, বোনকে একক শান্তি দিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় রেখা। তার এই আত্মদান গল্পের শীর্ষবিন্দু। যে আকাশ একদিন কথা বলতো, সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে মৌন বিষাদে ভরে ওঠে রেবার পৃথিবী।
বর্ণনার মিতব্যয়িতা, বক্তব্যের ইঙ্গিতধর্মিতা এবং চূড়ান্ত ব্যঞ্জনা ‘মৌন আকাশ’কে ছোটগল্প হিসেবে সার্থক করে তুলেছে।
এক কান্নার স্বাদ: সাংঘাতিকভাবে বন্যাকবলিত একটি এলাকার মানুষের জীবনে নেমে আসা দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে লেখা গল্প। স্বজন ও সহায়-সম্পদ হারানো পল্লিজীবনের বেদনার বিষাদগাথা বলা যেতে পারে। সঙ্গে অতিরিক্ত হিসেবে মিলেছে গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্যিক উপাচার। শুরুতে প্রকৃতির যে বিবরণ দিয়েছেন রিজিয়া রহমান, তা গল্পের কাহিনির প্রতি যেমন ইঙ্গিতবহ তেমনি বঙ্গপ্রকৃতির যথার্থ রূপধারণেও সক্ষম।
লালটিলার আকাশ: রিজিয়া রহমানের স্মৃতিচারণে জানা যায় মাস্টার্সের ছাত্রী থাকাকালে ‘লাল টিলার আকাশ’ গল্পটি প্রথম প্রকাশের সময় অশ্লীলতার অভিযোগের মুখে পড়েছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের ম্যাগাজিনে প্রকাশের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিলেন হলের প্রভোস্ট । পরিমার্জনে রাজি না হলেও বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর মধ্যস্থতায় গল্পটি অবিকল ছাপা হয়। তবে আজকের তো বটেই, সেই সময়ের বিচারেও গল্পটির কোথাও আপত্তিকর কিছু ছিলো বলে মনে হয় না। আরিফ নামের এক বাঙালি ডাক্তারের জবানিতে ব্রিটিশ ভারতের এক এ্যাংলো ইন্ডিয়ান পরিবারের অস্তিত্ব সংকটের গল্প।
ভাবতে ভালো লাগে, ব্রিটিশ ভারতের রক্ষণশীল একটি মুসলিম পরিবারে জন্ম নেওয়া ষাটের দশকে আবির্ভূত একজন নারী লেখকের প্রথম গ্রন্থ এটি, যেখানে ভাষা সাবলীল; গল্পের আবরণে যেখানে স্বাচ্ছন্দ্যেই পরিবেশিত হয়েছে ইতিহাস-নৃতত্ত্ব-প্রকৃতি-মৃত্তিকাতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ পর্যবেক্ষণশীল বিষয়াদি। প্রত্যেকটি গল্পেই প্রেম আছে। সেটা থাকাই স্বাভাবিক; কিন্তু প্রেম কোথাও প্রায় একা বা একঘেঁয়েমি আবহ তৈরি করেনি; প্রেম প্রকাশের পারিপার্শ্বিকতাগুলো নানামুখি বিচিত্রতায় ভরে উঠেছে। এবং সেই পারিপার্শ্বিকতাগুলো পাঠের সময় মনে হয়, এগুলো আরোপিত বা অন্যের দ্বারা লব্ধ কোনো বিষয় নয়, লেখিকার জীবনাভিজ্ঞতা থেকেই নেওয়া। সেই সময়ের একজন নারী লেখকের এই কৃতিত্বকে প্রশংসা করতেই হয়। আনুষঙ্গিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর বর্ণনায় রিজিয়া রহমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্রের আন্তঃবিশ্লেষণপ্রচেষ্টাও প্রশংসনীয়। কোনো কোনো গল্প হয়তো ছোটগল্প হিসেবে খুব উন্নত নয়; ভাষায় কিছুটা শৈথিল্যও হয়তো আছে; ঘটনাদির বর্ণনায় হয়তো আরও একটু মিতবাক হতে পারতেন রিজিয়া; কিন্তু তারপরও সার্বিক বিবেচনায় ‘অগ্নিস্বাক্ষরা’কে সফল রচনা বলতেই হবে। আর হ্যাঁ, গল্পকে দীর্ঘায়িত করতে পারা লেখকের বড়ো একটি গুণও বটে। তাছাড়া শেকড় সন্ধানী ও আধুনিকমনস্ক এই লেখিকা যে পরবর্তী জীবনে অনেক উল্লেখযোগ্য গল্পোপন্যাস উপহার দিয়েছেন, তার ভিত রচিত হয়েছিলো ‘অগ্নিস্বাক্ষরা’র গল্পগুলোর মধ্য দিয়েই।
রাইজিংবিডি/ঢাকা/১৯ আগস্ট ২০১৯/তারা
রাইজিংবিডি.কম
আরো পড়ুন